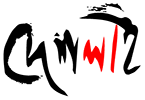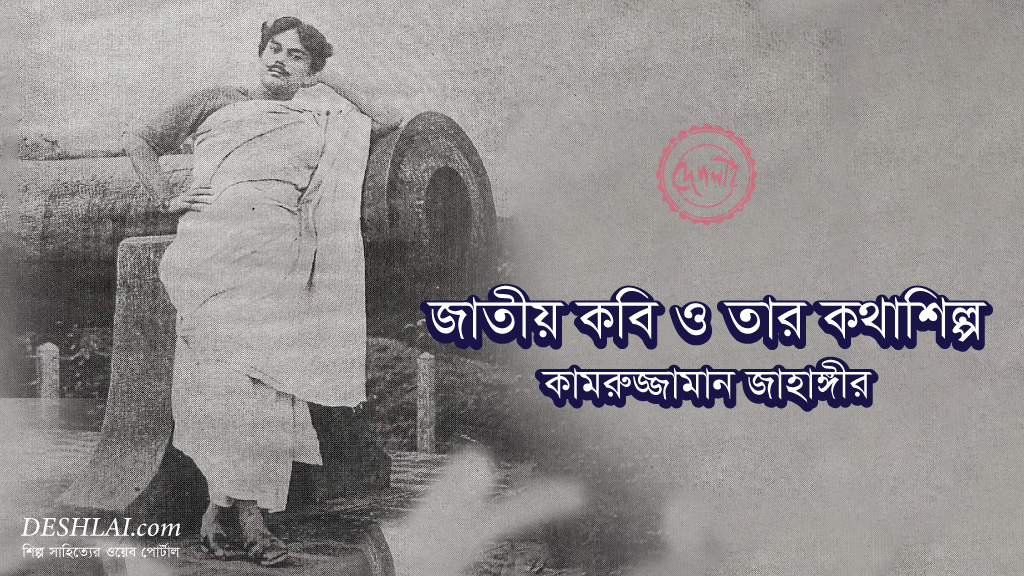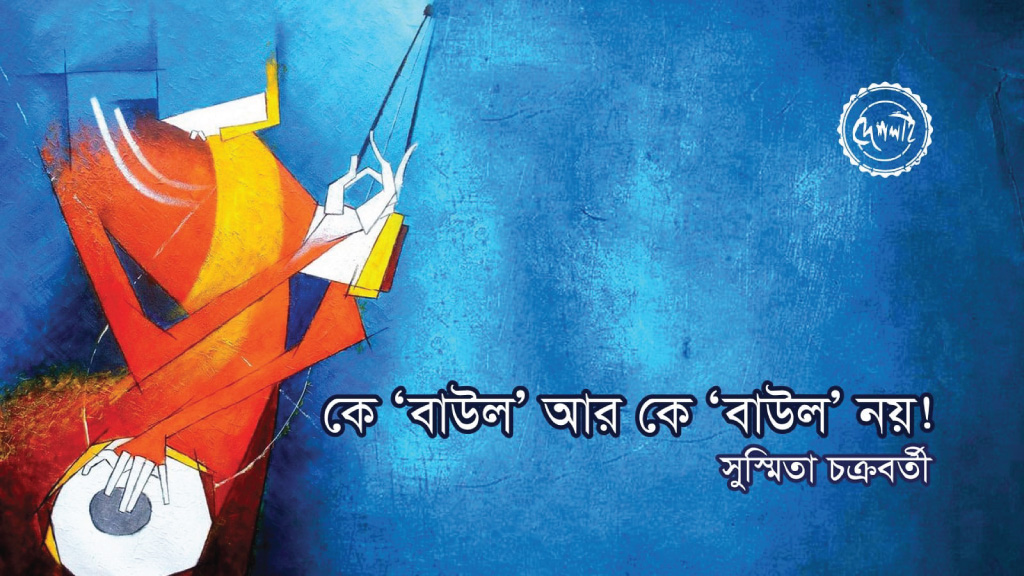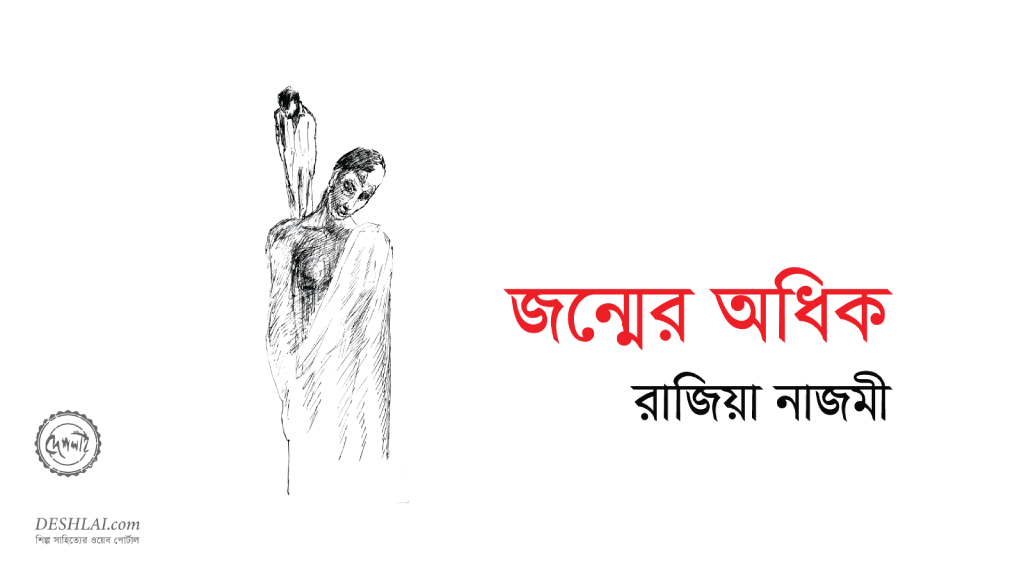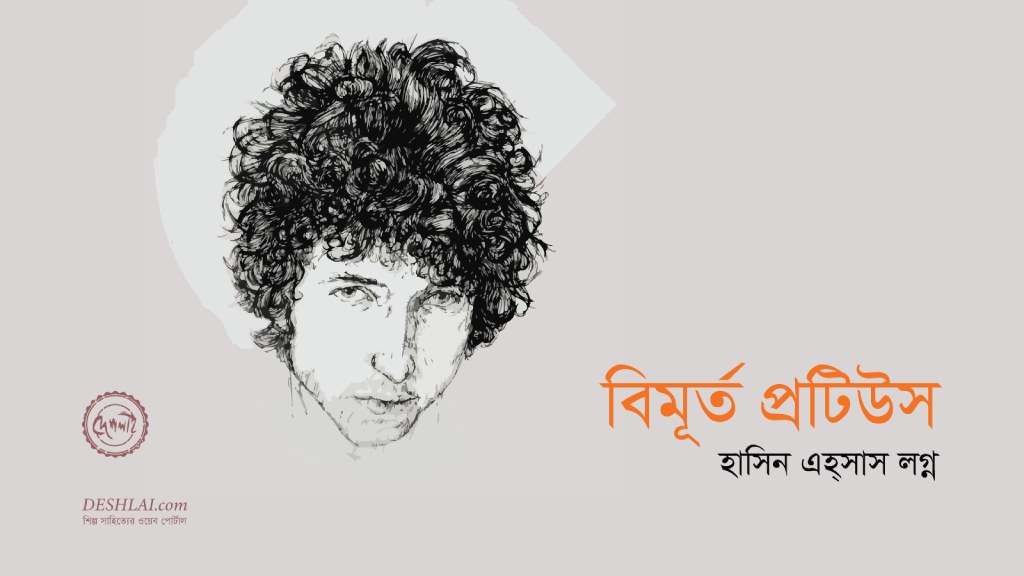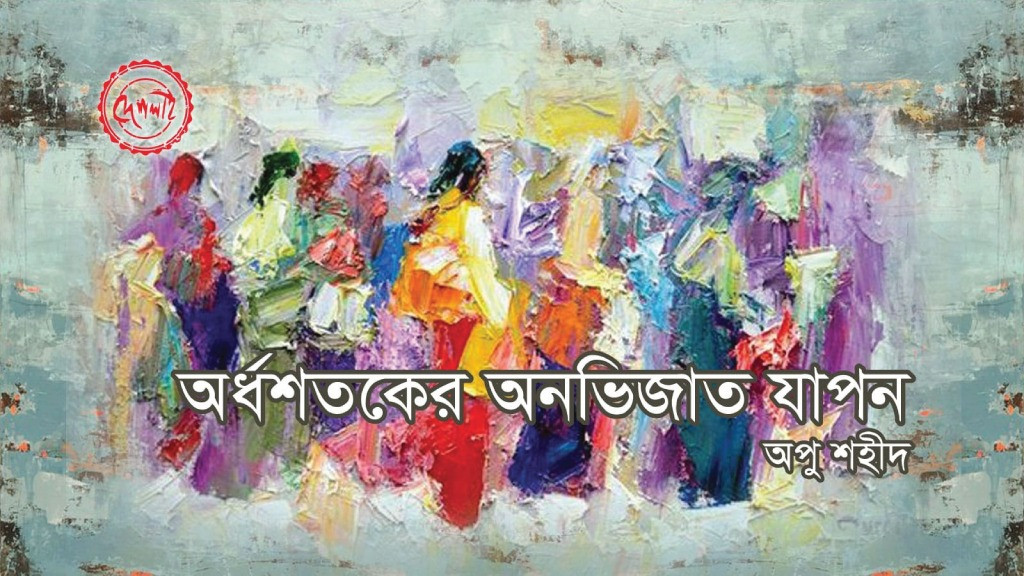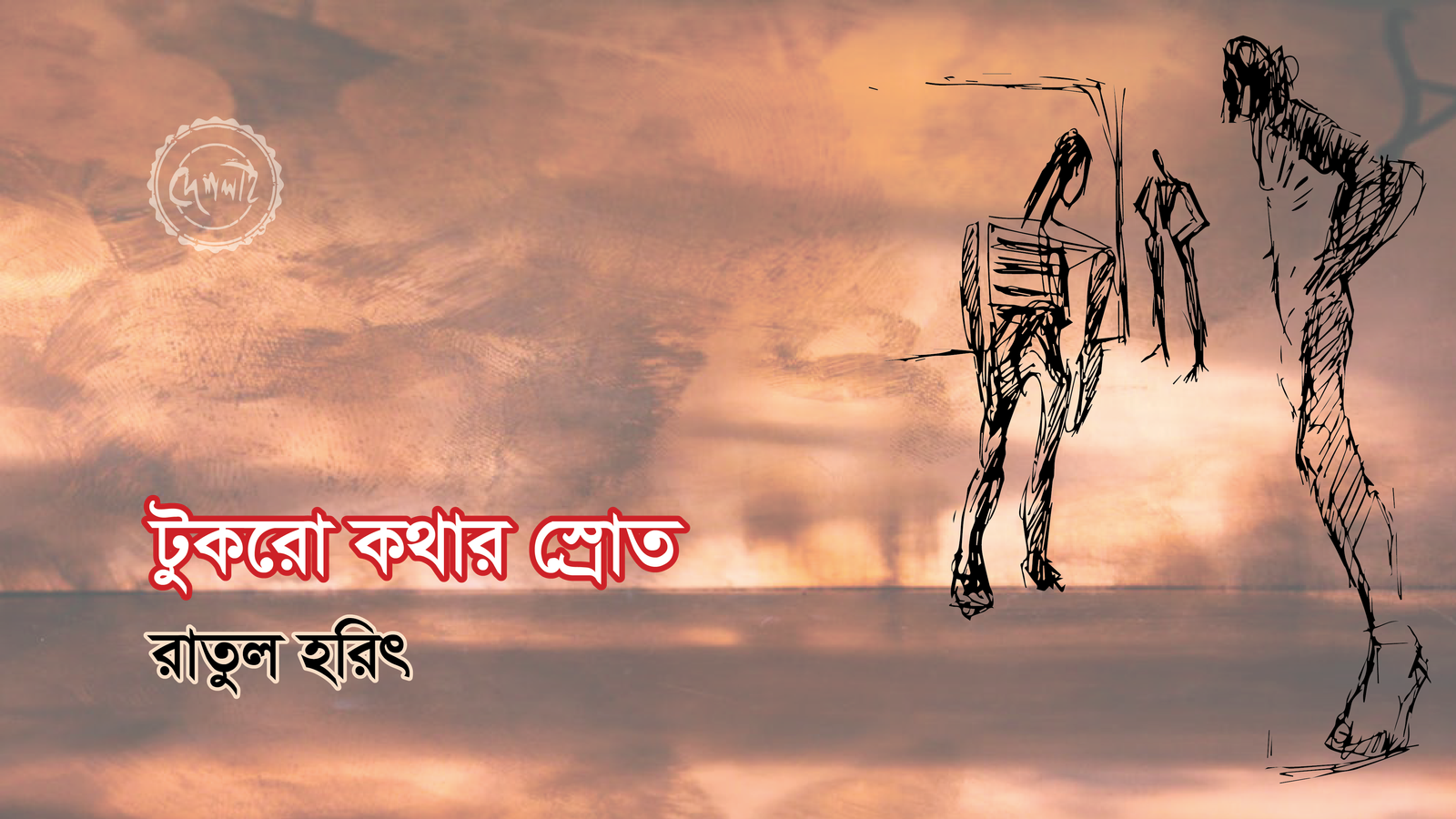
বর্তমান হচ্ছে ধনুকের তারে টানা তীরের
মতো। অতীতের টান ছাড়া ভবিষ্যতের দিকে সে ছুটতে পারে না। অতীত তাকে শক্তি দেয়, ভবিষ্যৎ
দেয় লক্ষ্য। আর বর্তমান সেই মুহূর্ত যেখানে শক্তি ও লক্ষ্য মিলিত হয়ে জন্ম দেয় ভবিষ্যতের
গতিপথ মানে আগামীর দিকনির্দেশ। অতীতের অভিজ্ঞতা ছাড়া ভবিষ্যত স্বপ্ন শূন্য। অতীত মায়ার
টান আর ভবিষ্যৎ স্বপ্নের আহ্বান। এই অতীত ভবিষ্যতের টানাটানিতে বর্তমান চর্চিত, অর্জিত
বর্জিত হয়ে রচিত হয়। জীবন সাধনা শিল্প-সাহিত্য অথবা কবিতা সব বর্তমানের নিগড়ে বান্ধা।
তীরের মতো জীবনও পিছনে না টানলে তার গতি জন্মায় না, সামনে ছুটতে পারে না। অতীতের অভিজ্ঞতা
ছাড়া ভবিষ্যতের পথ উন্মোচিত হয় না। বর্তমান- শক্তি সঞ্চয়ের জায়গা, সময়ের বিন্দু
যেখানে সংকট জমাট বাঁধে, সম্ভাবনা পথ খোঁজে, আর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক
প্রতিটি আন্দোলন এই বিন্দু থেকে জন্ম নেয়, গতি প্রকৃষ্ট হয়ে প্রগতিতে উত্তীর্ণ হয়।
মানুষের অস্তিত্বও সেই তীরের মতো—অতীতের অভিজ্ঞতা নিয়ে বর্তমান ছুঁয়ে ভবিষ্যতের
দিকে ধাবিত হয়। মানুষ এগিয়ে যাই এক পায়ে স্মৃতির ভার, অন্য পায়ে স্বপ্নের দিশা
নিয়ে।
কবিতায় সময়ের প্রবাহ থাকে, বহমান
সময়ের সারথি হয়েই কবিতাকে টিকতে হয়। কবিতা ইতিহাস নয়, আবার ইতিহাসের থেকেও বেশি
কিছু। কবিতা হচ্ছে সময়চেতনার অন্তর্লিখন ও অনুভবের সরল সরস ও গম্ভীর প্রতিবিম্ব, ইতিহাসের
চিলতে চিলতে ছায়াছবি কিংবা আলোকচিত্র। এই চিত্রসূত্র ধরেই ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা, আকৃতি-বিকৃতি
উন্মোচন হয়।
কবিতা মানবসভ্যতার প্রাচীনতম সৃজনশীল
অভিব্যক্তি। যুগে যুগে মানুষ তার অনুভূতি, স্বপ্ন ও সংগ্রামকে কবিতার ভেতর ধারণ করেছে।
কবিতা অনুভবের প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করে, ইতিহাস তথ্যের রেখাচিত্র আঁকে। আর প্রত্যেক
সৃজনকর্ম সময়ের ছাপচিহ্ন বহন করেই দীপ্ত হয়।
সময়ের প্রভাবে কখনও কখনও শব্দও তার
নিজস্ব অর্থ হারিয়ে ফেলে। তবুও ভাব শব্দাশ্রয়ী হয় আর শব্দ ভাবাশ্রয়ী হয়। বলা যায়-
ভাব শব্দের আশ্রয়ে শেকড় গাড়া আর শব্দ ভাবের ছোঁয়ায় মহিমান্বিত। ভাব আর শব্দের
ঝাপটা-ঝাপটি সহাবস্থানে বিষয়ের ভারসাম্য বিরাজ করলে আমরা ভরসা পাই। কবি জীবনানন্দ
দাশের কথায়- 'একজন কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার। কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাস
চেতনা, মর্মে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।'
যে কবিতা ভনিতায় বৃত্তবন্দী, আলো
আঁধারের রহস্যে আটকানো সেই কবিতা কতজনকে উদ্বুদ্ধ করে? কবিতার সহজবোধ্যতা সহজাত বার্তাবহ
আর দুর্বোধ্যতা আরোপিত। সাধারণ মেধা-মনন নিয়ে কাব্য জটিলতার এত জট ভাঙা সহজ নয়। আমাদের
চিন্তা ও অভিব্যক্তি গড়ে ওঠে সেই সাধারণ মানুষের তৈরি করা ভাষায়, যে ভাষায় আমাদের চলন–বলন ও মনন নির্মিত। কবির হাতে সেই ভাষা হয়ে উঠে ঐশ্বর্যমণ্ডিত, নানা
রূপ-রূপকে বৈচিত্র্যময়। তবুও সাধারণের উপযোগী হয়ে উঠবার দায় নিয়ে ক'জন কবি শিল্পী
আছেন?
যে কেউ সৃজনশীল বলে নিজেকে বিশেষ মনে
করে, গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সে অপাঙ্ক্তেয়। শিল্পী লেখক কবি দার্শনিক বিজ্ঞানী কেউই
সময় সমাজ রাজনীতির ঊর্ধ্বে নন। প্রত্যেকেরই সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে। কবিও এর ব্যতিক্রম
নন। তিনি সবার সঙ্গেই একা থাকেন, আবার একাকিত্বেও সবার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। একইসঙ্গে
উপস্থিত ও অনুপস্থিত, কাছে ও দূরে—এটাই কবিসত্তার দ্বন্দ্বময় অবস্থান। একখানে থেকেও
লক্ষ যোজন দূরে আবার লক্ষ যোজন দূরে থেকেও কবিকে একখানে এক হতে হয়। একাকিত্বের সঙ্গেই
সম্পর্কিত শিল্প অথবা সাধনা। অঙ্কুরের আকাঙ্ক্ষা ফুলেফলে, নদী সমুদ্রমুখী, আকাশ অসীমে
প্রসারমুখী, জীবনের উপলব্ধি প্রকাশে, আমি এভাবেই বুঝি শিল্পের সাধনা।
অভিধানের মৃত শব্দ সীমাবদ্ধ থাকে সুনির্দিষ্ট
অর্থে। কবির ছোঁয়া পেয়ে মৃত শব্দ চমকে ওঠে, প্রাণস্পর্শী হয়ে ওঠে শব্দোত্তর বহুবিধ
অর্থে তাৎপর্যে। শব্দ বাক্য ভাষায় যে কবিতা পড়ি আমরা আসলে তা পড়ি না। আমরা পড়ি
মন, চিন্তা-চৈতন্যের গহীন গোপন ইশতেহার। আর মনের আয়তন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের থেকেও বড়।
মনের কোন আদি অন্ত নেই। মন-ই যাবতীয় সৃষ্টির সূতিকাগার।
পৃথিবীর প্রতিটি ভাষার কবিতায় রচিত
হয় মনের পরিচয়। মানুষ যতটুকু প্রকাশ করতে পারে চলনে বা বলনে, মন তার চেয়েও অনেক
বেশি বহন করে। কিন্তু লিখতে বসে মন অনেককিছুই হারিয়ে ফেলে। হারিয়ে যতটুকু পায় ততটুকুই
ইতিহাস বেয়ে বেয়ে পৌঁছায় নতুন প্রজন্মের কাছে। মন ক্ষয়ে ক্ষয়ে ভাষাবদ্ধ হয়। ভাষা
ও মন সমার্থক হলেও ভাষার মৃত্যু হয়, মনের নয়। মন মৃত্যুহীন, অক্ষয়। মনের কারণেই
বিলুপ্ত ভাষা অনুদিত হয়ে বেঁচে থাকে অন্য ভাষায়, কবিতায়। আর কবিতা হয়ে মন বেঁচে
থাকে যুগ থেকে যুগে।
সুর-সংগীত কবিতা গল্প উপন্যাস চিত্র-নাট্য-নৃত্যকলা
ভাস্কর্য সব শিল্প সাহিত্যের বিষয়। সাহিত্য মানেই মনের পাঠচক্র। সাহিত্যচর্চা মানে
মন-মননের চর্চা, সাহিত্য পড়া মানে মনটাকে পড়া। এই সাহিত্য বা মন কি মানুষের কোন কাজে
আসে, মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে? করে না। করে না বলেই অধিকাংশ মানুষ শিল্প সাহিত্যের
বাইরেই বেঁচে থাকে। কিন্তু বাঁচার জন্যতো কাজ লাগে। কাজের প্রতি মানুষের আগ্রহ কোথা
থেকে আসে?
কাজের আগ্রহ আসে অস্তিত্বের সংকট থেকে।
কাজের সঙ্গে জীবিকা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। জীবিকা ছাড়া জীবিত থাকা যায় না, অস্তিত্ব
বিপন্ন হয়। এমন বিপন্নতায় মানুষের মন স্থির থাকে না। এই অস্থির মন নানা স্বপ্ন দুঃস্বপ্নের
ঢেউয়ে দোলে। এই দোলা থেকেই আগ্রহের জন্ম। একেক সময় একেক সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক
অর্থনৈতিক তাড়না মানুষকে টেনে নিয়ে যায় নানা কাজে, শ্রমে, সৃষ্টিতে কিংবা সংগ্রামে।
এই সংগ্রাম জীবনকে মর্যাদাপূর্ণ করে, অর্থবহ করে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষ নিজেকে
বদলায়, সমাজ-রাষ্ট্রকে বদলায়।
সমাজ এখন স্বার্থসিদ্ধির মঞ্চ, ভারসাম্যের
সার্কাস।আর মানুষ- সরকারি শুমারির খুচরো সংখ্যা অথবা ভোট ব্যালটের গুটি। অথচ মানুষের
সমাজ সঙ্গবদ্ধতার, সহাবস্থানের, সহযোগিতার, সহমর্মিতার, সুষম বন্টনের, দায়-দায়িত্ব
ভাগাভাগি করে নেবার জায়গা। সেই জায়গা এখন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর দমন-পীড়নের চারণভূমি।
মানুষের সমাজ এমন হবার কথা না। কিন্তু হয়েছে। একে আর সমাজ বলা যায় না। সমাজ এখন অন্যায়-অবিচার,
শাসন-শোষণ, খুন-ধর্ষণ, লুটপাট টিকিয়ে রাখার অবকাঠামো।
সমাজ-রাষ্ট্রের এই কাঠামোতে শাসকরা
নিশ্চিত— মানুষ সত্যিকার আগ্রহে জেগে উঠলে ক্ষমতা হাতছাড়া
হতে দেরি লাগে না। এই কারণে তারা শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি
ধর্ম, মিডিয়া—সব কিছু হাতের মুঠোয় এনে বলে- তোমার আগ্রহ শুধুমাত্র
স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখো, সার্টিফিকেট অর্জনের ফন্দিফিকিরে রাখো, চাকরিতে রাখো,
মোবাইল স্ক্রলে রাখো আর রাজনীতি থেকে দূরে থাকো।
সত্য হচ্ছে- রাজনীতি থেকে দূরে থাকা
মানুষের পক্ষে অসম্ভব। রাজনীতি থেকে দূরে থাকবার কোন উপায়ও জগতে নেই। রাজনীতি বাদ
দিয়ে জীবন হয় না। মানুষ মূলতঃ রাজনৈতিক জীব। প্রতিদিন আমাদের যত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস,
যত পছন্দ অপছন্দ, যত স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন—সব রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
এই রাজনীতির ভেতরে থেকেই আমরা গেয়ে
উঠি- তবুও জীবন যাচ্ছে বইয়ের জীবনের নিয়মে...। জীবনের এই নিয়ম তৈরি করে দেয় রাজনীতি।
রাজনীতির স্বতঃস্ফূর্ত স্ফুলিঙ্গ মানুষের বেঁচে থাকবার লড়াইয়ে দাবানল হয়ে জ্বলে
ওঠে। আগুন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চোখে থেকে চোখে।
চোখ খুলে দেখি তোমাকে, জগৎ সংসার,
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; বন্ধ করে দেখি নিজেকে। তখন স্থির হই, ধ্যনিষ্ঠ হই নিজের অন্তর্জগতে।
খোলা চোখে রঙ রেখা আলো স্পেস সব দেখি, চোখ বুজে দেখি মনের দরবারে এদের সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ
ও সমন্বয়। চোখ খুললেই চৌদিক, ইচ্ছেমতো যাওয়া যায়। মনোজগতে যেতে হলে চোখ বন্ধ করতেই
হয়। খোলা চোখ আমাদের দেয় গতি ও বিস্তার, বন্ধ চোখ আমাদের দেয় স্থিরতা ও গভীরতার
অন্তর্জগত— যেখানে বাইরের অভিজ্ঞতা রূপান্তরিত হয় চিন্তায়,
অনুভূতিতে এবং আত্মজিজ্ঞাসায়।
মনের আকার আকৃতি নেই, শারীরিক কোন
অবস্থাও নেই। মন নিরাকার। মনকে- দেখা যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। মন অদৃশ্য
অধরা অস্পৃশ্য হলেও তার উপস্থিতি পাওয়া যায় কর্মে মর্মে। মন ভালো নেই- বললেই অচল
অঙ্গসৌষ্ঠব। অদৃশ্য মন দৃশ্যমান দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে। মহাবিশ্বে ৬৮ ভাগ ডার্ক এনার্জি
(গুপ্তশক্তি) ২৭ ভাগ ডার্ক ম্যাটার (গুপ্তবস্তু) আর ৫ ভাগ বস্তুজগৎ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে
আমরা ৫ ভাগ দেখি ৯৫ ভাগ দেখি না। যা দেখি না তা মন আর যা দেখি তা দেহ। দেহের থেকে মনের
শক্তি অনেক বেশি।
মনের শক্তিতে বলিয়ান সৃজনশীল মাত্রই
একাকীত্বে একনিষ্ঠ হতে হয়। একাকীত্ব সাধারণের জন্য হীনমন্যতা, সৃজনশীলদের জন্য, কবিদের
জন্য উদযাপনের বিষয়। নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভেতরেই প্রত্যেকের জীবন-যাপন। যাপিত অভিজ্ঞতা
বোধে জারিত হয়ে সৃজন সুচিত হয়, কবিতা রচিত হয়। বহুতর ঘটনা রটনার সঙ্গে যুক্ত থেকে
বা না থেকেও এক বা একাধিক বিষয় নিয়ে কবিকে মুক্ত হতে হয়। যুক্ততা ছাড়া মুক্ত হওয়া
যায় না। মুক্তির তাড়না যুক্তির ভেতরেই। যুক্তির বাইরেও অনেক মহাজাগতিক সত্য থাকে
যাকে ধরতে হয় ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে।